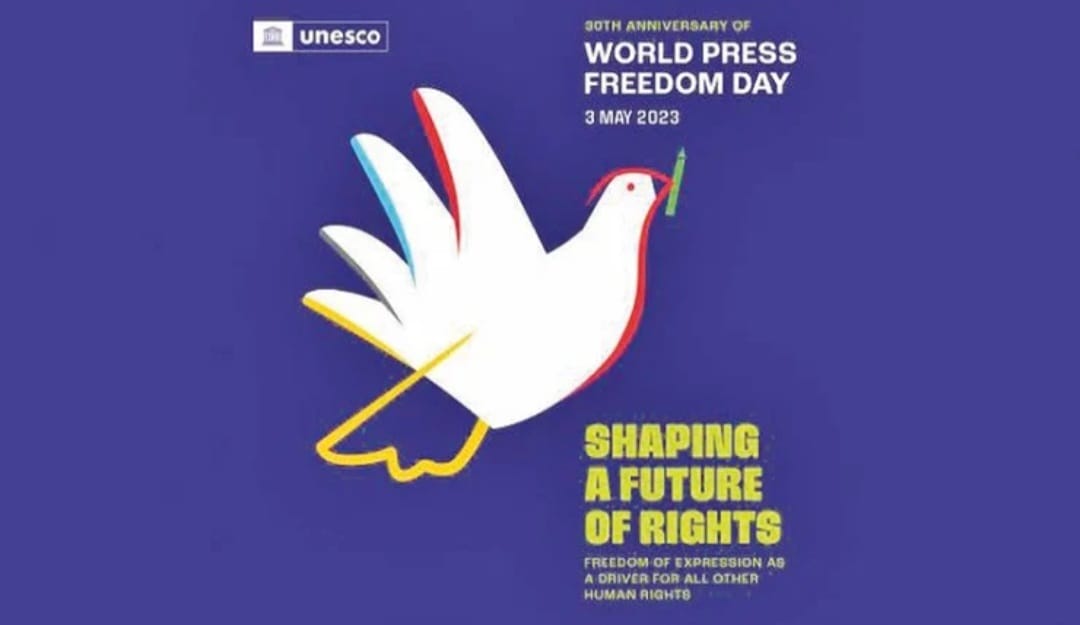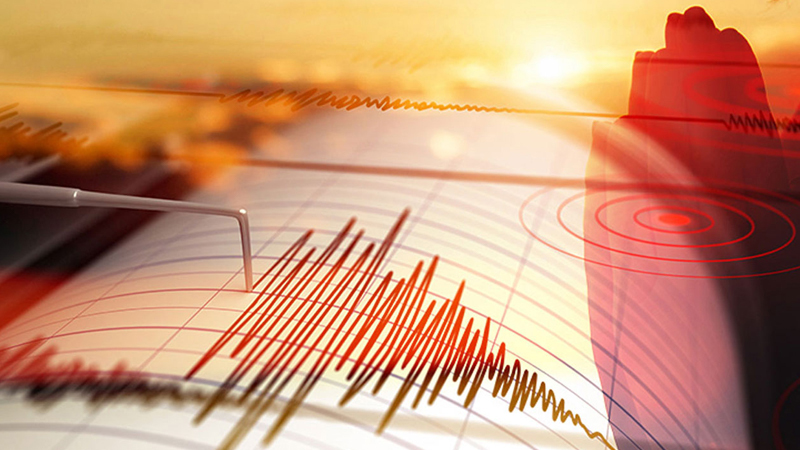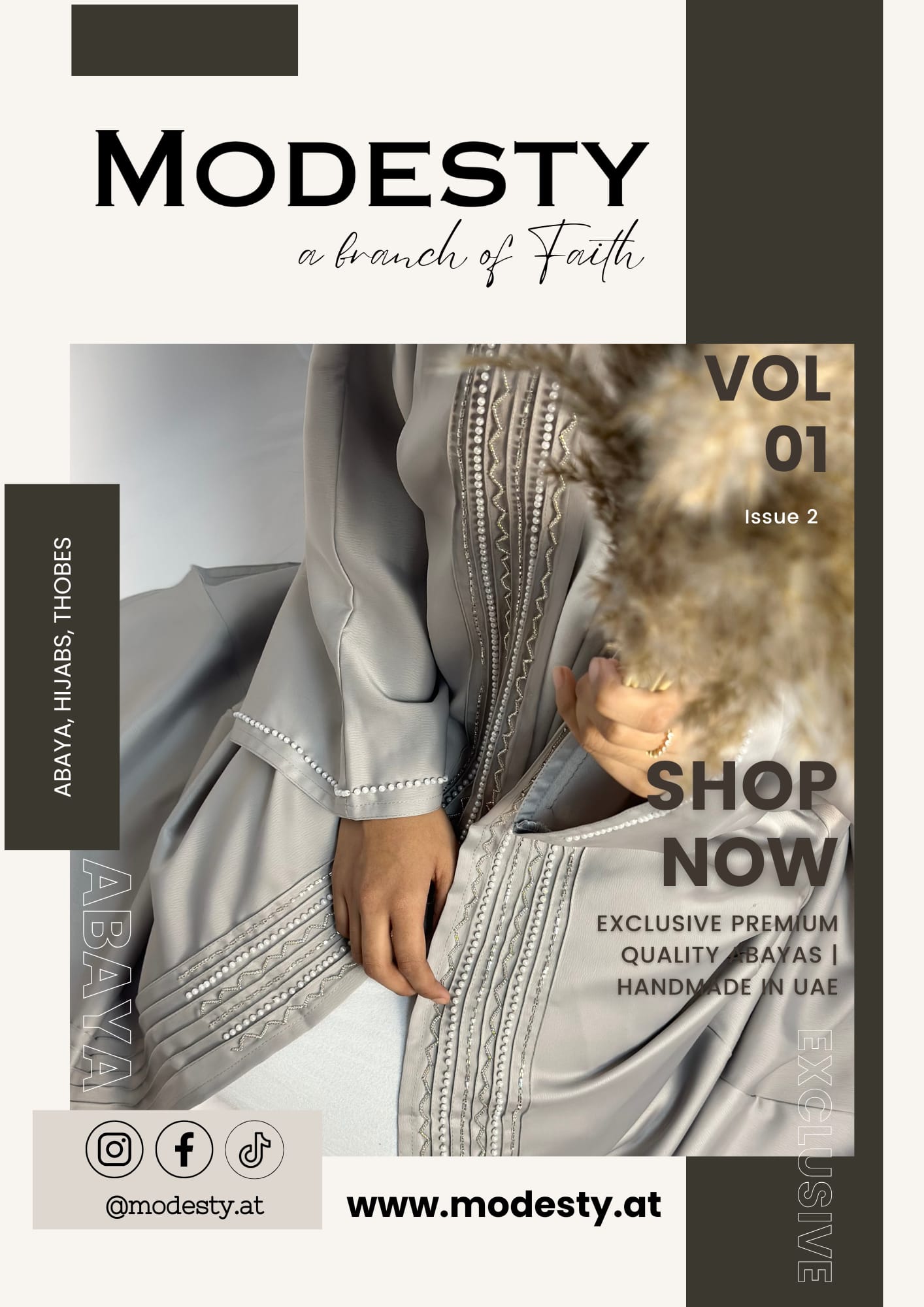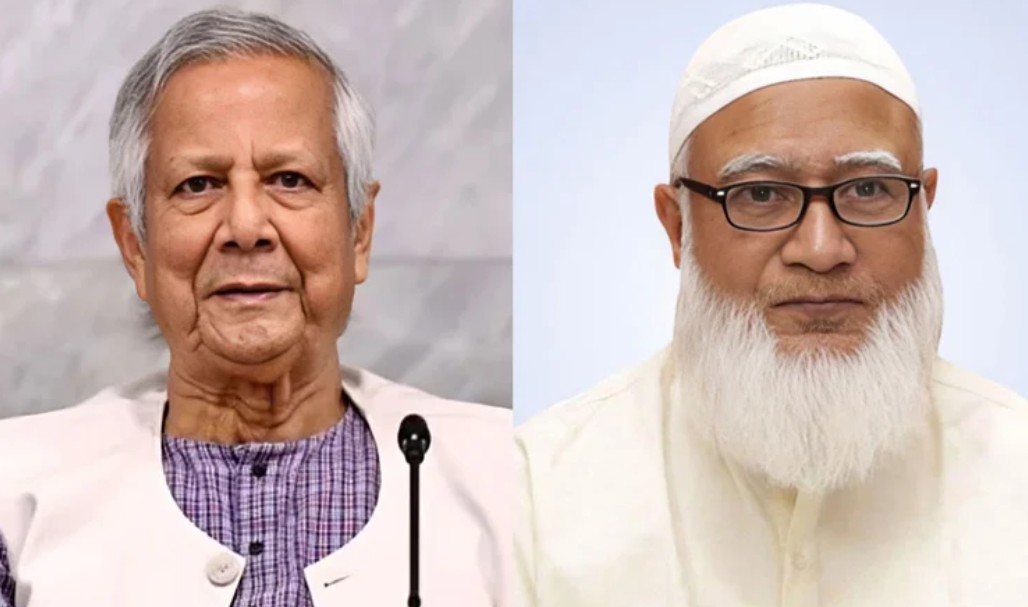এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সকল প্রকার মানবাধিকারের চালিকাশক্তি’

 কবির আহমেদঃ আজ ৩ মে বুধবার বিশ্বজুড়ে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত হচ্ছে। মুক্ত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে প্রতিবছর ৩ মে বিশ্বজুড়ে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত হয়ে আসছে।
কবির আহমেদঃ আজ ৩ মে বুধবার বিশ্বজুড়ে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত হচ্ছে। মুক্ত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে প্রতিবছর ৩ মে বিশ্বজুড়ে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত হয়ে আসছে।
অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে দেশের সাংবাদিকরা পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন।
উল্লেখ্য যে,১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনের সুপারিশ অনুসারে, ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ৩ মে তারিখটিকে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর থেকেই দিবসটি বিশ্বজুড়ে পালন করা হচ্ছে। এরপর থেকে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমকর্মীরা দিবসটি পালন করে আসছেন।
সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ, বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল্যায়ন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ও জীবনদানকারী সাংবাদিকদের স্মরণ ও তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় দিবসটিতে।

বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা ফ্রান্সভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)-এর করা সূচকে ২০২২ সালে বাংলাদেশ ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬২তম অবস্থানে ছিল। এর আগের বছর যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫২তম।
মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ১০ ধাপ পিছিয়ে যাওয়ার কারণ এবং এর ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কোন দিকে যাচ্ছে সে নিয়ে ব্যাপক কথা বলেছেন সম্পাদক, সাংবাদিক নেতা ও অ্যাকাডেমিশিয়ানরা। আমরা এবারের অবস্থান এখনও জানি না।
সংবাদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছে, বাংলাদেশের সূচকে অবনতির পেছনে সবচেয়ে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। এই আইনটি বর্তমানে সাংবাদিকদের হেনস্তা, দমন ও গ্রেফতারে ব্যবহৃত হচ্ছে।
এই আইনের ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে এবং প্রকৃত বিচার হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহৃত হচ্ছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই আইনে অনেক মামলা হয়েছে এবং সেই মামলাগুলোর অধিকাংশ করেছেন সরকারি দল বা তাদের সমর্থকরা।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অবশ্যই একটা নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই আইনের প্রয়োগ ঘটছে, যদিও আইনমন্ত্রীসহ অনেকেই বলেছেন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যেন এই আইনের প্রয়োগ না ঘটে সেটা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আমরা সবাই বুঝতে পারছি বাংলাদেশের গণমাধ্যম এক নতুন প্রেক্ষাপটের সামনে উপস্থিত।
এ কথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলাদেশে স্বাধীন মত প্রকাশের অবস্থা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। স্বাধীন সংবাদ পরিবেশন এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা কঠিন হয়ে পড়ছে। একদিকে জঙ্গি, দুষ্কৃতকারী, পেশিশক্তির দাপট, অন্যদিকে বিভিন্ন আইনের খড়গ সাংবাদিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে।
গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যম নাগরিকের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে, তথ্য জগতে তার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। মানুষ জানতে চায়, মানুষ সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চায়। আর সেখানেই গণমাধ্যমের ভূমিকা। নীতিনির্ধারক, আইনসভাসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘটাতে ভূমিকা রাখে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয় দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা। স্বাধীনতার আগে এবং পরে বাংলাদেশের গণমাধ্যম মানুষের প্রতিটি গণতান্ত্রিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সঙ্গে থেকেছে। বাংলাদেশে গণমাধ্যম নানা ঐতিহাসিক ঘটনায়, মানুষের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থেকেছে। দুর্নীতি, সহিংসতা ইস্যুকে অনেক সময় গণমাধ্যমই সবার আগে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছে।
বাংলাদেশের গণমাধ্যম চিত্রটি গত আড়াই দশকে বড় ধরনের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে। একসময় শুধু সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীল সমাজ এখন বাস করছে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্যের মহাসড়কে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সম্প্রচার সাংবাদিকতার যে দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল, তা আজ সম্প্রসারিত। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবাদে অনলাইন নতুন বাস্তবতা। তথ্যের একসময়ের যে একক প্রবাহ ছিল তার স্থলে চলে এসেছে মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের টু-ওয়ে গণমাধ্যম।
একদিকে সরকারের প্রচেষ্টায় মানুষের ভেতরে জন্ম নেওয়া উন্নয়ন স্পৃহা, অন্যদিকে জটিল রাজনীতি, উগ্রবাদের মতো বিষয়গুলো মোকাবিলা করে চলতে হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজকে। বলতে দ্বিধা নেই রাজনৈতিক কারণে বিভাজিত সাংবাদিক সমাজ রাজনীতি থেকেই বড় চাপটি বয়ে চলেছে। গণমাধ্যমের ওপর রাজনৈতিক চাপ নতুন নয়। তবে এখন আগের চেয়ে সেলফ সেন্সরশিপে বেড়েছে বহুগুণ। আমরা অনেক কিছু লিখছি, বলছি, অবাধে বলছি বা লিখছি, কিন্তু অনেক কিছুই প্রকাশ করছি না।
পুরোটা নয়, আংশিক সত্যের এই তথ্যপ্রবাহের যুগে এসে প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যম যে তথ্য বা কনটেন্ট উপস্থাপন করে, তার মালিকানা আসলে কার কাছে? সাংবাদিকের কাছে যিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন? নাকি গণমাধ্যম মালিকের কাছে? নাকি রাষ্ট্রে যার ক্ষমতা তার কাছে? এসব জটিল প্রশ্নের নানা ধরনের উত্তর হবে। তবু বলতে হবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দাপট, গণমাধ্যমের মালিক ও রাষ্ট্রের মিলিত নেক্সাসের মাঝেও জনগণের ভরসার এখনও শেষ ঠিকানা গণমাধ্যম। গণতান্ত্রিক অনেক প্রতিষ্ঠানের অকার্যকারিতায় বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের, মত প্রকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে গণমাধ্যমই এবং সেটা করছে সাংবাদিক সমাজ একটা লড়াইয়ে আছে বলেই।
এ দেশের একজন সাংবাদিককে এক নিরন্তর লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে তার দিন/ মাস/ বছর পার করতে হয়। এ লড়াই নিজের সঙ্গে, সঠিক সাংবাদিকতা সে করতে পারছে কিনা, লড়াই সহকর্মীদের সঙ্গে, লড়াই মালিকের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে, লড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে, এমনকি নিজের সাংবাদিক ইউনিয়নের সঙ্গে। প্রতিটি স্তরে তাকে বুঝে নিতে হয় কত কঠিন তার এই পেশা। রাষ্ট্র এবং রাজনীতির চাপ, করপোরেটের চাপ, সমাজের কট্টর মতামত, আইন ও প্রশাসনের অপব্যবহার, মিডিয়ার আপস—মত প্রকাশের স্বাধীনতার সামনে বিস্তর বাধা। সাংবাদিকদের মামলা দিয়ে হয়রানি করা খুব সাধারণ একটা ব্যাপার এখানে। মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় ব্যয় করতে হয় সম্পাদক ও সাংবাদিকদের। যারা নিজেদের উদ্যোগে সাংবাদিকতা করেন, তাদের ক্ষেত্রে এই বিপদ অতি প্রবল। বিশেষত দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে, তথাকথিত ‘জাতীয়’ সংবাদমাধ্যমের নাগাল ও নজর থেকে তারা অনেক দূরে।
চাকরির নিরাপত্তা নেই, ঠিকমতো বেতন হয় না বহু পত্রিকা, অনলাইন ও সম্প্রচার মাধ্যমে। গণমাধ্যম অর্থনীতি নতুন সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে নিয়মিত। সংবাদপত্র পাঠকের স্বল্পতা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাই এখন আরেক লড়াই। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস শোচনীয়ভাবে কমছে, কমছে দেশীয় টেলিভিশন দেখা। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক বিস্তার এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে, পাঠক বা দর্শক টেনে নেওয়ার পাশাপাশি এখন তারা গণমাধ্যমের আয়ের একমাত্র উৎস– বিজ্ঞাপনও ছিনিয়ে নিচ্ছে।
বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বড় পুঁজির প্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু তথাকথিত পুঁজি সাধারণ করপোরেট সংস্কৃতিও এই জগতে আনতে পারেনি। বাংলাদেশের খুব কম পত্রিকা, টেলিভিশন, বেতার বা অনলাইনের প্রাতিষ্ঠানিকতা দেখছি আমরা। গণমাধ্যম কর্মীদের রাজনৈতিক বিভাজন একটি বড় উদ্বেগের কারণ, সে কথা আগেই বলেছি। সরকারের সহযোগিতায় এবং একই সঙ্গে গণমাধ্যম কর্মীদের নিজেদের উদ্যোগে গণমাধ্যমসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে না উঠলে আমাদের সাংবাদিকতার মান বাড়বে না, আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না, আর্থিক অবস্থার কোনও বিকাশ দেখতে পাবো না নিকট ভবিষ্যতে।
মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, আসলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য দরকার নিজের ভূমিকার প্রতি গণমাধ্যম কর্মীদের আস্থা রাখা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, এমনকি সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোর উচিত একটা নিজস্ব আচরণবিধি তৈরি করে সে পথে চলা। গণমাধ্যমের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ গণমাধ্যমকে বাঁচাতে ভূমিকা চাই নাগরিক সমাজ থেকেও। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নাগরিক সমাজের নানা সংগঠন আছে, যারা গণমাধ্যম আক্রমণ হলে, বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ায়। এ দেশে তেমন সংহতির খুব অভাব। গণমাধ্যম লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্রকারদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে যেভাবে দাঁড়ায় তা কি দেখতে পাই আমাদের বেলায়?
বর্তমান বাস্তবতায় সংবাদমাধ্যমের জন্য তিনটি বিষয়কে প্রধানতম সমস্যা বলা যায়। এগুলো হলো, গণমাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য আইন ও প্রয়োগ, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, সরকার ও জাতীয় সমস্যা এবং উগ্রবাদ ও ধর্মান্ধতা। কিন্তু গণমাধ্যমের অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিকতার সংকট আমাদের কোথায় নিয়ে যায় সেটি দেখার অপেক্ষায় না থেকে একটু নিবিড় দৃষ্টি দেই কীভাবে সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। গণমাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সংকট ও সম্ভাবনার কথা বলে। গণমাধ্যম মানুষের স্বপ্ন পূরণের কথা বলে এবং বলেও যাবে সবসময়। কিন্তু আমরা জানি না নিজেদের আকাশে জমে থাকা মেঘ কাটবে কবে ?
নির্বাহী সম্পাদক (আন্তর্জাতিক)/ইবিটাইমস/এম আর